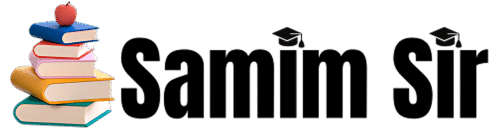ভাব সম্মিলন কবিতার বড় প্রশ্ন উত্তর Class 11। বিদ্যাপতি। একাদশ শ্রেণী দ্বিতীয় সেমিস্টার। Class 11 Vabsommilon Kobita Long Question Answer। WBCHSE
ভাব সম্মিলন কবিতার বড় প্রশ্ন উত্তর
১. ‘ভাব সম্মিলন’ কাকে বলে ? আলোচ্য পদটিতে রাধার আনন্দের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লেখো। ৫
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 ভাব সম্মিলন: কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পর আর বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি। কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনরা রাধার বিরহ কাতরতা দেখতে পারছিলেন না। তাই বাস্তবে না-হলেও তাঁরা রাধাকৃষ্ণের মানসিক মিলনের ব্যবস্থা করে দেন, এই মিলনই হল ভাব সম্মিলন।
👉 শ্রীরাধিকার আনন্দের চিত্র: আমাদের পাঠ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদে শ্রীরাধিকা তাঁর সখীকে জানিয়েছেন, তাঁর আনন্দের কোনো সীমা নেই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাবলোকে আবার ফিরে এসেছেন। আসলে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন তাঁর মনের মন্দিরে বসবাস করেন। কৃষ্ণ দূরে থাকার সময় পাপী চাঁদ তাঁকে যতটা দুঃখ দিয়েছে, এখন প্রিয়তম কৃষ্ণের মুখদর্শনে তাঁর ততটাই সুখ অনুভূত হয়েছে। দীর্ঘ বিরহ পর্যায়ে শ্রীরাধিকা অনুভব করেছেন কৃষ্ণই। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই মহামূল্যবান ধনরত্ন পেলেও তিনি আর কৃষ্ণকে দূরদেশে পাঠাবেন না। তাই শ্রীরাধিকার ভাবজগতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মিলনে মনে আনন্দ প্রকাশিত হয়েছিল।
২. “চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর” – কে, কাকে মাধব বলেছেন ? উক্তিটির তাৎপর্য কী ? (২+৩)
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 বক্তার পরিচয়: আলোচ্য উক্তিটির বক্তা হলেন শ্রীরাধিকা।
👉 যাকে বলেছেন: আলোচ্য উদ্ধৃতিতে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে মাধব বলে উল্লেখ করেছেন।
👉 উক্তিটির তাৎপর্য: ভাবসম্মিলনের পদে বিরহ-বিচ্ছেদে কাতর শ্রীরাধিকা তাঁর মনে মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি উপলব্ধি করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন মথুরায়। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে তাঁকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু শ্রীরাধিকা এতদিন পর উপলব্ধি করেছেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর শারীরিক বিচ্ছেদই সম্ভব। মানসলোকে তাঁরা অভিন্ন সত্তা। রাধিকার ভাবলোকে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর প্রাণনাথ। আর সেই মুহূর্তেই তাঁর বিরহ-বেদনা দূর হয়ে গিয়েছে। এখন তাঁর মনোজগৎ কৃষ্ণময়। তিনি ভাবছেন চিরদিন কৃষ্ণ তাঁর মনের মন্দিরে বিরাজ করবেন। অর্থাৎ, কৃষ্ণ চিরদিন শ্রীরাধিকার হৃদয়ে বিরাজ করবেন।
৩. ‘সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি’ – সুজন কে ? তাঁর দুঃখের কারণ কী ? তাঁর দুঃখের অবসান কীভাবে ঘটেছিল ? (১+২+২)
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 সুজন কে ? : আলোচ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদে সুজন বলতে শ্রীরাধিকাকে বোঝানো হয়েছে ।
👉 সুজনের দুঃখের কারণ: শ্রীরাধিকাকে ফেলে রেখে প্রিয় কৃষ্ণ গিয়েছেন মথুরায়। সমগ্র বৃন্দাবন আকুল হয়ে উঠেছে রাধিকার বিরহ-কাতরতায়। বৃন্দাবনের বক্ষে নেমে আসা মায়াবী চাঁদের জ্যোৎস্নালোক সেই বেদনাকে দ্বিগুণ করেছে। প্রিয়-বিচ্ছেদে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। প্রিয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদে শ্রীরাধিকা দুঃখে কাতর হয়েছিলেন। সেই অতীত দুঃখ-স্মৃতি প্রসঙ্গেই আলোচ্য উদ্ধৃতিটির অবতারণা।
👉 দুঃখের অবসান : পাঠ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণ চিরতরে মথুরা চলে যাওয়ার পরেও শ্রীরাধিকা তাঁর ভাবলোকে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পেয়েছেন। এর ফলে কৃষ্ণের আর চলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি চিরকাল শ্রীরাধিকার অন্তরেই বিরাজ করবেন। তাই সুজন অর্থাৎ শ্রীরাধিকার দুঃখের অবসান ঘটেছে। দীর্ঘ বিরহকাল যাপনের পর প্রিয়ের সঙ্গে ভাবলোকে মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন শ্রীরাধা।
৪. ‘ভাব সম্মিলন পদটিতে শ্রীরাধাকে কবি বিদ্যাপতি কীভাবে চিত্রিত করেছেন ? ৫
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 রাধার অপরিসীম হৃদয়বেদনা উপলব্ধি করে ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলন পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতি ভাবলোকে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছেন।
👉 রাধার চরিত্র চিত্রায়ণ: আলোচ্য পদে সখীর কাছে রাধা যে আনন্দ অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন তার থেকে স্পষ্ট যে রাধা, কৃষ্ণ ছাড়া অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণ ছাড়া রাধার জীবন তাৎপর্যহীন। সে কৃষ্ণপ্রেমে একনিষ্ঠ। বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ চিরতরে চলে গিয়েছেন মথুরায়। রাখা দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করেও কৃষুধ্যানে মগ্ন হয়ে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন প্রিয় কৃষ্ণের সান্নিধ্য। অর্থাৎ বিদ্যাপতির মতোই রাধা অনুভূতিপ্রবণ। চিরআকাঙ্ক্ষিত মানুষকে মনের মন্দিরে লাভ করে অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছেন তিনি। দীর্ঘ বিরহের সময় তাঁর শেষ হয়েছে। তাই তিনি সখীর কাছে কৃষ্ণপ্রেমের অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করেছেন। কবি বিদ্যাপতির রাধা চঞ্চল। বিরহ তাঁর কাছে অন্তহীন সত্য নয়। দুঃখকে অতিক্রম করে কাঙিক্ষত সুখের নাগাল পেয়েছেন রাধা। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে প্রেমের মাধুর্যে তিনি বিশ্বাসী নন, রাধা ভাবলোকে প্রিয়সঙ্গ লাভ করেন চিরন্তন প্রেমসৌন্দর্যে তাঁর আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বিদ্যাপতির রাধাকে ‘সত্বয়’, ‘লীলাময়ী’ আখ্যা দিয়েছেন। লীলাময়ী রাধার অন্তহীন প্রেমতুয়া পাঠ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।
৫. “কি কহব রে সখি আনন্দ ওরা”- এই পদটি কোন পর্যায়ের পদ ? কে মন্তব্যটি করেছেন ষ? ‘ওর’ শব্দের অর্থ কী ? এই আনন্দের কারণ নিজের ভাষায় লেখো। (১+১+১+২)
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 এটি হল ভাবোল্লাস ও মিলন পর্যায়ের পদ।
👉 বিদ্যাপতি রচিত ‘ভাব সম্মিলন’ পদে কৃষ্ণ প্রেমিকা শ্রীরাধা উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
👉 ‘ওর’ শব্দের অর্থ সীমা-পরিসীমা।
👉 ‘মাথুর’ বা বিরহ পর্যায়ে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা রাধার মধ্যে তীব্রভাবে বেজেছিল-“এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।”
কিন্তু ভাবসম্মিলনের পদে এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে রাধা ভাবময় জগতে তাঁর মনের মধ্যেই কৃষ্ণকে উপলব্ধি করেছেন। প্রিয়তমের মুখদর্শনে তিনি সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম করে গিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি কেউ তাঁকে মহামূল্যবান রত্নসামগ্রীও দেয়, তবুও তিনি তাঁর প্রিয়তমকে দূরদেশে পাঠাবেন না। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে বিদ্যাপতির রাধার উত্তরণ ঘটেছে এক নবতর আনন্দময় জগতে। সেই সীমাহীন আনন্দের উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত অংশে প্রকাশিত হয়েছে।
৬. “পাপ সুধাকর যত দুখ দেল ?”- ‘সুধাকর’ শব্দের অর্থ কী ? সুধাকরকে ‘পাপী’ বলা হয়েছে কেন ? ‘যত দুখ’ বলতে এখানে কীসের ইঙ্গিত করা হয়েছে ? (১+২+২)
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 সুধাকর শব্দের অর্থ: ‘সুধাকর’ শব্দের অর্থ হল চাঁদের আলো।
👉 সুধাকরকে পাপী বলার কারণ : বিদ্যাপতির লেখা ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতায় আমরা দেখি প্রিয়তম কৃষ্ণের বিরহে রাধিকা যখন দুঃখে কাতর, তখন চাঁদের মায়াবী জ্যোৎস্না যেন আরও বেশি করে তাঁকে কৃষ্ণের কথা মনে করাচ্ছে। অথচ তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে পারছেন না। শ্রীরাধিকার বিচ্ছেদ বেদনা দ্বিগুণ করে তোলার জন্য সুধাকরকে পাপী বলা হয়েছে।
👉 ‘যত দুখ’ প্রসঙ্গ: শ্রীরাধিকাকে ফেলে রেখে প্রিয় কৃষ্ণ গিয়েছেন মথুরায়। সমগ্র বৃন্দাবন আকুল হয়ে উঠেছে রাধিকার বিরহ- কাতরতায়। বৃন্দাবনের বুকে নেমে আসা মায়াবী চাঁদের জ্যোৎস্না লোক সেই বেদনাকে দ্বিগুণ করেছে। চাঁদের প্রতি তাই শ্রীরাধিকার মনে বড়োই আক্রোশ জন্মেছে। প্রিয়-বিচ্ছেদে তিনি কাতর হয়ে পড়েছেন। প্রিয়- মিলনের পূর্বে রাধার এইরূপ অবস্থার বর্ণনাতেই ‘যত দুঃখ’ শব্দবন্ধটির অবতারণা।
৭. “পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেলা”- ‘পিয়া-মুখ’ কার ও তা দেখে কে সুখ লাভ করেছে ? তাঁকে দেখে কীভাবে সুখ পাওয়া গেল ? (১+১+৩)
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 ‘পিয়া-মুখ’ কার ? : ‘পিয়া-মুখ’ বলতে পাঠ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রীর কথা বলা হয়েছে।
👉 যে সুখলাভ করেছে : ‘পিয়া-মুখ’ দর্শন করে স্বয়ং শ্রীরাধিকা সুখ লাভ করেছেন।
👉 যেভাবে সুখ পাওয়া গেল : বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ বহুদিন যাবৎ মথুরায় অবস্থান করছেন। তাঁর শূন্যতা বৃন্দাবনকে মলিন করেছে। বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদর্শনে আকুল হয়ে উঠেছে। আর তাঁর প্রাণাধিক প্রেমিকা শ্রীরাধিকার অবস্থা বড়োই করুণ। দুষ্ট চন্দ্র বারবার কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে তাঁকে আরও বেশি কাতর করছে। দীর্ঘ দিন কষ্ণকে না দেখার ফলে রাধার মনে কৃষ্ণের জন্য প্রবল বিরহ যন্ত্রণা জেগে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎই ভাবসম্মিলনের অনুভূতিতে শ্রীরাধিকা দেখেন, তাঁর মানসলোকে শ্রীকৃষ্ণ যেন সর্বত্র, সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাই শ্রীরাধিকার মনে কৃষ্ণকে দেখতে না পাওয়ার দুঃখ মুহূর্তে মুছে গিয়েছে। তাই মনোজগতের ভাবনায়, কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে শ্রীরাধিকা সুখ লাভ করেছেন।
৮. “পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ডেল” – কার, কখন এই উপলব্ধি ঘটে ? তাঁর এই মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করো । (১+১+৩)
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 আলোচ্য কবিতায় এই উপলব্ধি হয় শ্রীরাধিকার।
👉 যখন এই উপলব্ধি: কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে, প্রেমময় চাঁদের কিরণ রাধাকে কৃষ্ণের কথা মনে করাত। কিন্তু শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে কাছে পেতেন না। দীর্ঘ বিরহ শেষে ভাবলোকে কৃষ্ণকে কাছে পেলে শ্রীরাধিকার এই উপলব্ধি হয়।
👉 মন্তব্যের কারণ: শ্রীরাধা যখন প্রিয় কৃষ্ণের বিরহে কাতর, তখন চাঁদের মায়াবী জ্যোৎস্না যেন কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে রাধার বিরহ যন্ত্রণাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিরহ যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। শ্রীরাধিকা পরম প্রিয়ের সন্ধান পেয়েছেন ভাবলোকে। তাই তাঁর দুঃখের অবসান ঘটেছে। বৃন্দাবন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ চিরতরে চলে গিয়েছিল মথুরায়। ফলে রাধার বিরহ গভীরতর হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি রাধার এই হৃদয়যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার এই বিরহজনিত দুঃখ বেদনাকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে রাজি নন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি। কৃষ্ণের মথুরা গমনের সত্যতাকে মেনে নিয়ে, শ্রীরাধার তীব্রতর হৃদয়বেদনা অনুভব করে, বিদ্যাপতি ভাবলোকে তাঁদের মিলন সম্পন্ন করিয়েছেন। কৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময় হয়ে রাধা মানসলোকে মিলিত হয়েছেন প্রিয়ের সঙ্গে। মনের মন্দিরে কৃষ্ণকে পেয়ে আর হারানোর ভয় নেই তাঁর। অপরিসীম আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন রাধা। বিরহকালে পাপী চাঁদের আলো তাঁকে যত দুঃখ দিয়েছিল, ভাবলোকে প্রিয়কে চিরতরে পেয়ে ঠিক ততখানিই সুখের অনুভূতি হয়েছে রাধার।
৯. “অচির ভরিয়া যদি মহানিধি পাই/তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই” – ‘পিয়া’ দূর দেশে গিয়েছিলেন কেন ? বক্তা শ্রীরাধিকা তাঁকে আর দূরদেশে পাঠাতে রাজি হননি কেন ? (২+৩)
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 দূরদেশে যাওয়ার কারণ: শ্রীরাধিকা তাঁর প্রিয় কৃষ্ণর দূরদেশে অর্থাৎ মথুরায় যাওয়ার কথা বলেছেন। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছিলেন রাজা কংসকে বধ করার উদ্দেশ্যে।
👉 রাজি না হওয়ার কারণ: প্রিয়তম কৃষ্ণ দূরদেশে চলে গেলে শ্রীরাধিকা প্রিয় বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাণনাথ, তাঁরা অভিন্ন সত্তা। তাই শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি রাধিকাকে মৃতবৎ করে তুলেছে। মণিহারা ফণীর ন্যায় তিনি ছটফট করছেন। তাই নিঃসঙ্গ রাধা এরপর যখন কৃষ্ণকে নিজের ভাবজগতে পুনরায় ফিরে পান, তখন তিনি অনুভব করেন কৃষ্ণই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই কোনো কিছুর বিনিময়ে শ্রীরাধিকা অমূল্য কৃষ্ণকে দূরদেশে পাঠাতে রাজি নন। কারণ প্রিয়বিরহ তাঁর পক্ষে পুনরায় সহ্য করা অসম্ভব, মৃত্যুর সমান। আঁচল ভরে মূল্যবান ধনরত্ন পেলেও রাধা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্রীকৃষ্ণকে আর দূরে যেতে দেবেন না।
১০. “শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।” – প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করো। ৫
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 প্রসঙ্গ: আলোচ্য অংশে কবি বুঝিয়েছেন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, কেবল শ্রীরাধিকার প্রেমিকই নন, তিনি তাঁর ত্রাতাস্বরূপ। রাধার জীবনে কৃষ্ণের গুরুত্ব কতখানি, তা বোঝাতে বিদ্যাপতি এই মালা রূপক অলংকার ব্যবহার করেছেন।
👉 ব্যাখ্যা: দীর্ঘদিন কৃষ্ণবিচ্ছেদ শূন্য শ্রীরাধিকাকে উন্মাদিনী করে তুলেছিল। আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমকে মানসলোকে পেয়ে তাঁর আনন্দের আর সীমা নেই। ভাবের অতিশয্যে ভেসেছেন শ্রীরাধিকা। সখীর কাছে সেই আনন্দ ব্যক্ত করছেন, নানা অলংকার-অভিধায় ভরিয়ে তুলছেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর কাছে কতটা মূল্যবান, তা বোঝাতে কী বলবেন, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তিনি সখীকে বলছেন, ওড়না বা উত্তরীয় যেমন শীতের প্রকোপ থেকে শরীরকে রক্ষা করে তেমনই শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধিকার অসময়ের রক্ষক, আবার প্রবল গ্রীষ্মের দিনে সুশীতল বাতাসের মতো শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার জীবনে আনেন প্রশান্তি। কৃষ্ণ যেমন ছাতার ন্যায় প্রতিকূলতার ধারা বর্ষণ থেকে রাধিকাকে রক্ষা করেন, তেমনই কৃষ্ণই তাঁর জীবন নদীর নৌকা। দুর্গম ভব পারাবারের কান্ডারি। রাধার জীবনে তিনি নিশ্চিন্ত আশ্রয় সুখ। অর্থাৎ রাধার জীবন জুড়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। এ কথাই আলোচ্য অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।
১১. “ভপয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি” – ‘বরনারি’ শব্দের অর্থ কী ? কাকে ‘বরনারী’ বলা হয়েছে ? তাঁকে ‘বরনারি’ বলার কারণ কী ?
উত্তর –
👉 বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত “বৈষ্ণব পদাবলী” সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘ভাব সম্মিলন’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি গৃহীত হয়েছে।
👉 ‘বরনারি’ শব্দের অর্থ: কবিতার ভণিতা অংশে ব্যবহৃত ‘বরনারি’ শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ রমণী।
👉 যাকে বলা হয়েছে: আলোচ্য পদে শ্রীরাধিকাকে ‘বরনারি’ বলা হয়েছে।
👉 ‘বরনারি’ বলার কারণ: পাঠ্য ‘ভাব সম্মিলন’ পদে শ্রীরাধিকাকে বিদ্যাপতি বরনারি বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ শ্রীরাধিকা হলেন শ্রীকৃষ্ণের সখীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
(ক) একমাত্র শ্রীরাধিকাই হ্লাদিনী শক্তির অধিকারী। তাই অভিন্ন সত্তা রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ কখনোই বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়।
(খ) বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু বা নায়িকা হলেন শ্রীরাধা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপা অর্থাৎ তিনি সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের আনন্দ আস্বাদনের শক্তিস্বরূপ। রাধা, কৃষ্ণেরই অংশ। রাধার মাধ্যমেই কৃষ্ণ, প্রেমে মগ্ন হন। তিনি আর রাধা কোনো পৃথক সত্তা নন। কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তিকে বলা হয় হ্লাদিনী শক্তি, রাধা কৃষ্ণের আরাধিকা।
শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যযুগে বিভক্ত হয়েছে। প্রাক-চৈতন্যযুগের সাহিত্যে রাধার প্রেম ছিল নই লৌকিক অনুভূতির। কিন্তু উত্তর চৈতন্যযুগের রাধাপ্রেম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং বৈয়বসাহিত্য অনুসারে ব্রজগোপিনিদের মধ্যে রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমে সকল বাধা অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তিনি কুল-মান মর্যাদা সর্বস্বত্যাগ করেছেন। বৈয়ব রসশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘উজ্জ্বলনীলমণি’-তে বলা হয়েছে, চন্দ্রাবলী ও রাধার মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠা। রাধার প্রেমই কৃষ্ণের সৌন্দর্য, মাধুর্যকে বিকশিত করেছে।
আরও পড়ুন –
তেলেনাপোতা আবিষ্কার গল্প প্রশ্ন উত্তর
YouTube – Samim Sir